দীর্ঘ কবিতা
জাদুঘর থেকে বলছি
অনিরুদ্ধ আলম
পর্ব ২।।
পিচ্ছিল বাতাসে নীলগাইয়ের গাম্ভীর্য-মাখা রঙিন ঘুড়ির দুরন্তপনা তোলপাড় করে রোদের ডালপালাকে। অধীর কম্পাঙ্কে বেড়ে-ওঠা ওরকম উদ্দামতায় আমারো একটুকরো কৈশোর ছিল। নাটাই থেকে ধারে-নেয়া আন্তরিক বীরত্বকে পুঁজি করে হাওয়াকে ভয় দেখায় অহংকারী ঘুড়ি। তেড়ে যায় চিলকে। চিল আরো দূর-আকাশে কেন্দ্রিভূত হয়। পেলব অক্ষে লীন হয়ে ঝিলমিলে তিল হয়। আহা! সে কী আনচান! চিলের কৈশোর কি চিরায়ু?
বুঝেছি – কৈশোরে চঞ্চল ছিলাম। কিন্তু জানা হয় নি ব্যাকুলতা কাকে বলে? জানা হয় নি – যখন পাহাড় বেয়ে উত্তাল হাতির লোমশ দল দুদ্দাড় নেমে আসে, তখন সেই পাহাড়ের বুকে কেমন হৃৎকম্প শুরু হয়! বাড়ি থেকে ছেঁড়াখোঁড়া ঝোপটা পেরুলেই মাঠের হাট। তারপরেই মানসী নদী। নদীর ঘুমঘুম পুনরাবৃত্তির জল আমার চোখে মাখতাম। একটা ছিপ নৌকো সবসময় ঘাটেই বাঁধা থাকত। একদিন খুব ভোরে কুয়াশায়-অস্পষ্ট নদীর ঘাটে এলাম। ছিপনৌকোটা নিয়ে ভাসতে লাগলাম। যাব নির্জলা ডাকিনীর দ্বীপে। এই নদীটা পুবে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আছে এক ডাকিনীর দ্বীপ। সে দ্বীপ বড়ো ভয়ঙ্কর। সেখানে কোনো মানুষ যেতে পারে না।
ডাকিনীর আছে সাতটি হীরের মণি। একবার ওকে বধ করতে পারলে সেই সাত রাজার ধন হস্তগত হবে। কিশোরবেলায় এমনই গল্প শুনেছিলাম নানীর কাছে। তো আমি চলছি তো চলছি। পুঞ্জাক্ষির ব্যধিহীন উজ্জ্বলতায় ম ম করে ওঠা মানসী খুব চওড়া নদী নয়। স্রোতের বিচারাধীন জলগুলো অবিরল নিরুদ্বেগ। নাও ভাসতে লাগল ঢিমেতালে ময়ূখমালার কোটর চিরেচিরে। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়হয়। ডাকিনী দ্বীপের দেখা নেই। নদীর দুই ধারে সেই একই গ্রাম। একই দৃশ্য। কাশের মতো শাদা নদী, নদীর মতো রুপোলি মেঘে চলছে রঙের বাঁকবদল। ঝিরঝিরে বাতাসের কারাবাসে ক্লান্তি হয়ে উঠল অমীমাংসিত ঘুমের আচ্ছন্নতা।
আচ্ছন্ন হয়ে কতবার ভেবেছি বড়ো হয়ে একদিন জাহাজের নাবিক হব। সাতসমুদ্র পাড়ি দেব। সিন্দাবাদের মতো এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে ঘুরব। তবে সিন্দাবাদ তার সমুদ্রভ্রমণে যে ভুলগুলো করেছিল তা আমি করব না। পইপই করে তার সবগুলো ভ্রমণকাহিনী পড়ে নিয়েছি। তাই ওই ভুলগুলো কিছুতেই আমার ক্ষেত্রে আর হবার নয়। যদি কোনো অবাঞ্ছিত দ্বীপে নামার পর এক খুনখুনে বুড়ো এসে আমার ঘাড়ে চাপার সবিনয় অনুরোধ করে তা আমি কোনোভাবেই গ্রাহ্য করব না। বরং যত পারি তাকে বন থেকে আঙুর জোগাড় করে এনে দেব। তবু ঘাড়ে চাপা নয়!
আমার ঘাড়ে একবার খুব ব্যাথা পেয়েছিলাম। গাছ থেকে পড়ে এমনটা হয়। তখন আমার বয়স দশ কী এগারো। বেশ মনে আছে। পাশের বাসার শিরি আপু একদিন বিচলিত দুপুরে আমার কানেকানে বলল, ‘ঋজু, চল্ নাজমাদের বাগানে গিয়ে জাম পাড়ি। ওদের জামগাছের জামগুলো খুব ডাঁসাডাঁসা আর পেকে কালো টসটসে হয়েছে। তুই গাছে উঠে পেড়ে দে। আমি আচাড় বানিয়ে দেব। খুব মজা হবে।’ জামের ডাল ছিল খুব নাজুক। আমি ডাল ভেঙে মাটিতে ধপ্পাস! এরপর অনেক দিন বিছানায় পড়ে ছিলাম। ঘাড়ের অমার্জিত ব্যথায় তেমন কষ্ট পাই নি। কষ্ট পেয়েছিলাম শিরি আপুর সঙ্গে প্রায় দু’ মাস বনেবাদাড়ে ঘুরতে না পারার কারণে। শিরি আপু ছিল আমার চেয়ে একবছরের বড়ো। তাতে কী। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল দারুণ পিঠাপিঠি। খুব ভালো পিঠে বানাতে পারত সে। এখনো কোনো পিঠে খেতে বসলে শিরি আপুর কথা হৃদয়ে শাখাপ্রশাখা মেলে।
দেখেছি – ভাপা পিঠের মতো কবোষ্ণ মায়া ডুমুরের বুকে ফোটে। জলন্ধরীর প্রজ্ঞাকে পুঁজি করে পাতারা ক্রমে হলুদ হয়। কখনো ঘন হয়ে আসে সব্যসাচি জলের শরীর বৃষ্টির উত্তাপে। একবার ভেবেছিলাম বৃষ্টিগানের স্বরলিপি লেখব। চেষ্টাও করেছি। কিন্তু ঘুরেফিরে সে-এক কথা ‘টাপুরটুপুর। টাপুরটুপুর।’ তবুও এখনো যখন একাগ্র চিত্তে বৃষ্টির সঙ্গীত শুনি কক্ষনো একঘেয়েমি মনে হয় নি। আসলে বৃষ্টির পেশীবহুল ধ্বনি হৃদয়ে জমে থাকা সকল ধুলো ধুয়েমুছে সাফ করে দেয়।
ধুলো-হাওয়ার কলহ – সে তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কলহে-কলহে কেটে গেল বেতসপাতা ও নদীর দিনগুলো। তপ্ত রুটির মতো তেঁতে আছে মাঠ আর জমির আবাদহীন শোভা। আততায়ী খরার কাল কবে শেষ হবে? প্রাচীন প্রেতাত্মার দুর্ধর্ষতা দেখিয়ে সারা গাঁওকে ছেয়ে রেখেছে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। ন্যূনতম ষড়রিপুর ব্যগ্রতায় ক্লিষ্ট হয়ে ঈশানে মেঘ খুঁজেখুঁজে যখন সকলে হয়রান, তখন আমি স্লেটে আঁকি বৃষ্টিস্নাত বিকেল। আচমকা ঝড়ের আভাস দিয়ে মেষের প্রগাঢ়তায় মিশমিশে পশমি বৃষ্টি নেমে এল। নিস্তেজ হয়ে পড়া বাড়ি-ঘেঁষা পথটা উচ্ছ্বাসে সোঁদা ঘ্রাণ ছড়াতে লাগল। গাছের ডাবগুলো ঝরনার রমণে কেমন চকচক করছে। আগের বাসার কল্পনাদি খুব ভালো গান জানেন। তার ঘর থেকে বর্ষাসঙ্গীত ভেসে আসছে। কিন্তু বিধি বাম। ঘণ্টাখানেক পরেই বৃষ্টি উধাও।
আয়নার সশস্ত্র স্বচ্ছতা নিয়ে উটকো বৃষ্টির পানি উঠানে জমে আছে এদিক-ওদিক। নিয়ত দগ্ধক্ষতে জর্জরিত হাঁড়িতে জেঁকে-বসা কালোর প্রভাকে মূলধন করেছে মেঘেরা। কেমন গম্ভীর জোটবদ্ধ আকাশে-আকাশে! আলটপকা সুচের মতো তীক্ষ্ণ আলোর ব্যঙ্গাত্মক তরবারিতে দ্বিখণ্ডিত হল মেঘ। পুরো গাঁও তরল রোদ্রে ডুবে গেল। চনমনে মুড়ির চঞ্চলতা হয়ে রোদ্দুর প্রফুল্লতার পরাগায়ণ ঘটাতে লাগল বাতাসে এলোমেলো। দুটো চড়ুই সেই কখন থেকে হরিণ শাবকের সচকিত চোখ নিয়ে উঠোনে ঘুরঘুর করছিল। ঘাড় ফিরিয়ে সন্তর্পণে ইতিউতি চেয়ে চট করে সিকির মতো চকচকে পানিতে নেয়ে নিচ্ছে নিমেষে। ভাবখানা এমন উঠোন-মালিকের অনুমতি ছাড়া জলকেলি করাতে বড়ো কোনো অপরাধ হয়ে গেল না তো! তবুও তাদের এ খেলা চলল ক্ষণেক্ষণে ছড়িয়ে চৈতন্যের উষ্ণতা।
উষ্ণ লবণের বুদবুদ-স্বাদ বুকে নিয়ে সাগরের বালিরা মুছে দেয় অনাহূত পদচিহ্নের শিল্প। আবারো আসবে কি লাল কাঁকড়ার দিন? এখন একনামে পরিচিত হাতে-ফোস্কাপড়া মানুষের উপকূল। বৈদ্যরা হঠাৎ করে কোথাও অচিন প্রদেশে ঘুরতে গেছে। জাল বুনবার জন্যে যে-অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন তা কিনে নিয়ে গেছে চিরতরে পার্শ্ববর্তী বাণিজ্যনগরের মুৎসুদ্দীরা। ধূ ধূ সৈকতে শুধু জল আর বেলার সঙ্গম। গাঙচিল ডলফিনের লুকোচুরিতে উঁকি দিয়ে বলে, ‘এসো দলেদলে। কোথাও কেউ নেই।’ ময়ূরপুচ্ছের মতো জলের ফোয়ারা ছুটল দিগ্বিদিকে।
বর্ষা আসলেই মনেমনে ময়ূরী পুষি। পেখম-আবেশে কদম পরিপূর্ণ হয় নিষ্পলক হলুদ নাটকীয়তায়। প্রবাদের মতো তুমি এসে আমাকে বললে, ‘চলো বৃষ্টিতে ভিজি!’
কাকভেজা সজনের ডাল সজীবতার নিশ্চুপ উচ্চতায় নিজেকে মেলে ধরে। তাহলে কেমন করে অবশিষ্ট থাকে ধূসরতার গ্লানি? হাজার-দুয়ারি শূন্যতার অধিকর্তা কাহ্নপার সহজিয়া পদাবলির তৃষ্ণা নিয়ে আমিও নির্লজ্জের মতো জানালার কাছে বসি। লাবণ্যের মেলে দেয়া লাল শাড়িটা এখনো তাদের উঠোনের তারে জল-হাওয়াতে দোল খাচ্ছে। ওর লেখা চিঠিটা বারোতম বারের মতো খুলে ধরলাম। ওতে লেখা, ‘ভাইয়া, সময় পেলে জানালার পাশে এসো। আমাকে দেখতে পাবে!’
জোছনারাতে আমি দেখতাম আমার জানালায় একটি নয় দুটো চাঁদ উঁকি দিচ্ছে।
গহীন জোছনায় গাঁয়ের পথ ধরে কেউ হেঁটে চলে যায় নগরের দিকে। কাচের গুড়োর মতো নাগরিক আলো মিশে আছে নিষ্পাপ ধুলোর শরীরে। শরীর কেটে যায়। রক্ত ঝরে না। ঝরে পড়ে অব্যক্ত তারাদের সদ্ভাব ঘুম।
ঝুমকো ঘুমের আদলে বর্ধিষ্ণু হতে দেখেছি চিলেকোঠাদের ছায়া। ছায়ার আপাদমস্তক সংশয়ে দ্রবীভূত ক্রোধ, মায়া, ঘৃণা আর প্রেম এসে জমাট বাঁধে ললিত গড়নের পাষাণের ফুসফুসে। কোন কপট হৃদয় তার চোখ বেঁধে দিয়েছে? ‘আমাকে দেখত দাও!’ প্রমিথিউসের উত্তরসূরী সে-চিৎকার আকাশে-বাতাসে প্রতিধবনিত হয়ে নৈঃশব্দ্যের অনিন্দ্য ভাস্কর্যে পরিণত হল। কেউ কি ভুলেও সে আর্তচিৎকার তার একান্ত উচ্চারণ বলে দাবি করল না? কখনো করবে কি? তবে কি মানুষ মানুষের যোগ্য হয়ে উঠেছে? এক হাতে ন্যায়-অন্যায়ের অসঙ্কোচ তুলাদণ্ড। অন্যহাতে বুক-চেতানো মশাল। এমন মননশীল কারুকাজ আভিজাত্য এনে দেয় শহরের চেতনাসমৃদ্ধ জীবনপ্রবাহে।
অভিনয়ের কাছে বন্দকগ্রস্ত জীবনচক্রে ব্যবসা-প্রতিভূরা গ্রামে আসে প্যাটেন্ট-ছাড়া প্রাচীন প্রজাতির কোনো ধানের খোঁজে। কিংবা বিশ্ব বনায়ন দিবসে একবার তো গাঁয়ে আসা চাই-ই চাই! পাতার ক্লোরোফিলে, পাখির কাকলীতে আমাদের অস্তিত্বকে জারিত হতে দিতে হয়।
তুমি বলেছিলে, ‘পাখিকে খাঁচায় বন্দি করা আর পাখির ছবি ক্যামেরাবন্দি করে ঘরে ঝুলিয়ে রাখা– দুটো একই কথা।’
কেন তুমি এরকম অদ্ভুত কথা বলেছিলে? তা জানা হয় নি। তবে মনেমনে এই দার্শনিক তত্ত্বের একটা ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। পাখি খাঁচায় বন্দি থাকলে তার সুডৌল স্বাধীনতা খর্ব হয়। নিসর্গ হারায় তার প্রাত্যহিক সৌন্দর্য। অন্যদিকে যে-ড্রয়িংরুমে পাখির বিশাল ছবি শোভাবর্ধন করে, সেখানে হয়ত একসময় কোনো বন, জঙ্গল অথবা একটি সুঠাম বৃক্ষ ছিল; ছিল পাখির অভয় ডেরা। পাখিদের ঘর ভেঙে আমাদের ঘর গড়ি। আবার সে-ঘরেই ঝুলিয়ে রাখি তাদের ঢাউস ছবি। অন্ধ আলোর প্লাবন আমাদের ঘরদোর-করিডোর আর সংগ্রহশালাকে গ্রাস করছে উচ্চাকাঙ্ক্ষী দক্ষতায়। এ কেমন আলো মুখোশ খুলে গেলেই কোঁকড়ানো আঁধার দেয় হাতছানি! মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত লাবণ্যরা সবিশেষ মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে জনারণ্যে-তৈরি মঞ্চে ক্ষণেক্ষণে। কল্পবিজ্ঞান থেকে উঠে-আসা নতুন প্রজাতির তুষার-দেয়াল আমাদেরকে বুঝি যথেষ্ট প্রবোধ দেবে সৌন্দর্য-চেতনার অন্য মাত্রায়!
পাখিকে বনের সৌন্দর্য হিসেবে বিবেচনা না-করে তাকে ড্রয়িংরুমের সজ্জাঘটিত উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা একটি পৌনঃপুনিক ভুল। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে একটি শুদ্ধ অপরাধও বটে!
কোনো এক-সনির্বন্ধ ধ্যান আমাকে অপরাধী করেছে। বৃক্ষ হতে চেয়েছিলাম। বৃক্ষ হই নাই! (চলবে…)


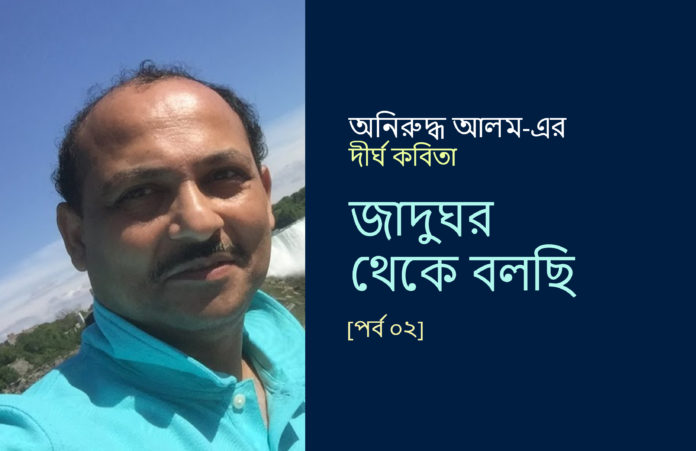





দীর্ঘ কবিতা জাদুঘর থেকে বলছি-ভালোই লিখছো। শেষ পর্ব পড়ে সম্পূর্ণ মতামত দেবো। পড়ে বেশ ভালো লাগছে।
এমনিতে তোমার লেখার তুলনা হয়না। তুমি সত্যি খুব ভালো লেখো। সাবলীল ভাষা। সকলের মনে ধরবেই।
ধন্যবাদ দাদা। অনেক-অনেক শুভেচ্ছা রইল। ভালো থাকবেন অবিরল।